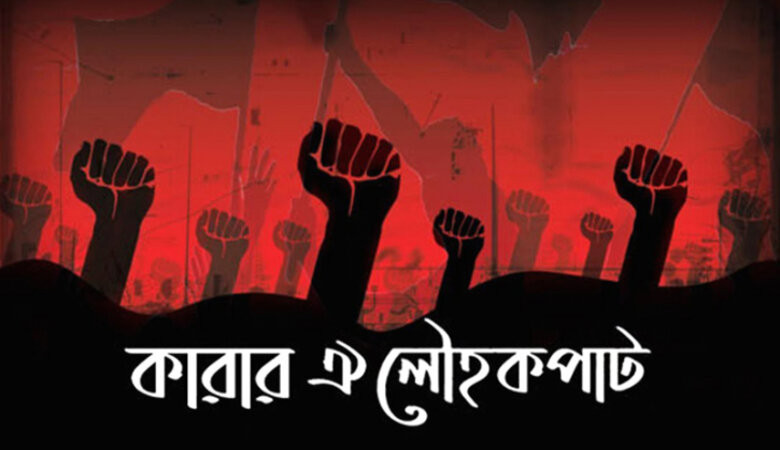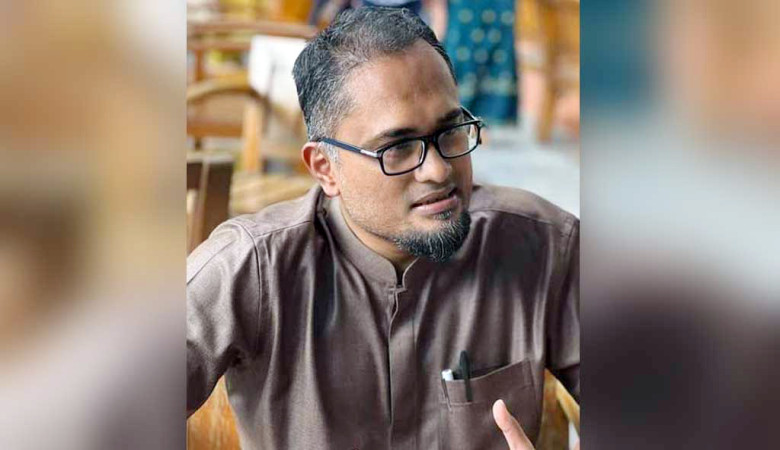দেবব্রত নীল
১৯২২ সালের ২০ জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত ‘বাঙ্গলার কথা’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ‘ভাঙার গান' শিরানামে ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম ২০টি বাংলা গানের অন্যতম ৩২ চরণের এই গানটিতে অভিনব, অভূতপূর্ব শব্দ, চিত্র ও বক্তব্যের এক মহামিলন ঘটিয়েছে। জেলখানার লৌহকপাট ভেঙে ফেলে লোপাট করার আহ্বান জানিয়ে কবি তরুণদের হাতে গাজনের বাজনা তুলে দিয়েছেন। অত্যাচারী অপশক্তিকে পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য মহাদেবের প্রলয়–বিষাণ বাজিয়ে পাগলা ভোলার মতো ছুটে আসার জন্য দুহাত তুলে ডাক দিয়েছেন। যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ: যথা-দুন্দুভি, হায়দরী হাঁক, গাজনের বাজনা, শিবের প্রলয়দোলা, কাল-বোশেখীর সমর্থন তাদের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে। এ গানের প্রত্যেকটি শব্দ, চিত্রধ্বনির আবেদন শত্রুর দুর্গ ভাঙার। এ গানে কবি পৌরাণিক শক্তির উপর আশ্রয় করে মহাপ্রলয়ের ডাক দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানে বেশ কিছু পৌরাণিক চরিত্রকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
তরুণ ঈশানঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানের পঞ্চম চরণে তরুণ ঈশান শব্দটি উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঈশান হচ্ছে ভগবান শিবের আরেক নাম। ঈশান শব্দের মূল ‘ঈশ’ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঈশ অর্থ জগৎকে শাসন করার অদৃশ্য শক্তি। ঈশান ও ঈশ্বর সমার্থক। শিবের পাঁচটা রূপ আছে। এই রূপ পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত। এই পঞ্চরূপের অন্যতম হলো ঈশান। ঈশান হচ্ছে শিবের পঞ্চম রূপ, যা উপর দিকে চেয়ে থাকে। ঈশান উত্তর-পূর্বদিকের রক্ষক। শিবের পবিত্র সংখ্যা হলো পাঁচ। শিবের শরীর পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা গঠিত। এগুলোকে বলা হয় পঞ্চব্রাহ্মণ। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই পাঁচটি রূপ পঞ্চভূত,পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মহাপরাক্রমশালী মহাদেব কৈলাশে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকলেও বিমূর্ত রূপ ধারণ করে জগতের সকলের কল্যাণ সাধন করে থাকেন। মহাদেব ধ্যানরত অবস্থায় সর্বদা উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে মুখ করে অবস্থান করেন। উত্তর প্রান্তের দিকে আছে সমৃদ্ধি, ধন-সম্পদ আর প্রাচুর্যতা। অপরদিকে পূর্ব প্রান্তের দিকে বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানের বিকাশ বিরাজমান। উত্তর এবং পূর্ব এই দুই দিককে মিলন কেন্দ্র বানিয়ে মহাদেব জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনায় রত থাকেন বলে তাকে ঈশান নামে অভিহিত করা হয়। অগ্নি, জল,বায়ু, পৃথিবী, আকাশ এই পঞ্চরূপে মহাদেব সর্বত্র বিরাজ থাকেন। মহাদেবের আকাশ রূপের প্রতিমূর্তি হলো ঈশান।
[পৌরাণিক অভিধান, দশম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৬ পৃষ্ঠা -৫৫]
নজরুল চিরসুন্দর ঈশানের উপমা ব্যবহার করে নবীন ও তরুণদের সত্য পথে সাহসী থেকে নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস অর্জন করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। শোষকের অত্যাচারে বিপ্লবীদের রক্তরঞ্জিত কারাগারই হলো পূজার পাষাণ বেদি। প্রাকৃতিক শক্তি ভয়ংকর কালবৈশাখীর প্রলয় রূপে শিব যেরকমভাবে অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে, কবি প্রত্যাশা করেছেন দেশপ্রেমিক তরুণরা ঠিক সেভাবেই শক্তি ও সাহসের উন্মত্ত প্রকাশ ঘটিয়ে উদ্যম, স্পর্ধা এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে আসুক।
প্রলয় বিষাণঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানের ষষ্ঠ চরণে প্রলয় বিষাণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মহাদেব প্রলয়ের পূর্বে বিষাণ বাজিয়ে ধ্বংসের সূত্রপাত করে থাকেন। প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মুক্ত হয়ে মহাদেব সংহারক মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। ধ্বংসলীলা করার সময় তার শরীর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে অন্যরূপ ধারণ করে। তিনি ভয়ঙ্কর বৃষের মতো লোহিত বরাহের রূপ ধারণ করে সংহার করেন। গলায় রুদ্রাক্ষ, এক হাতে ডুগডুগি আর অন্যহাতে থাকে ত্রিশূল। মহাদেবের এই ত্রিশূল তিনটি শক্তির প্রতীক- জ্ঞান, ইচ্ছা এবং সম্মতি। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক এই তিন লোকের সংহার করার জন্য মহাদেব এই ত্রিশূল ধারণ করে। সাধারণভাবে দেখলে দ্যুলোক হলো মস্তক, ভূলোক হলো দেহ আর অন্তরীক্ষ হলো আত্মা, মন। কবি মহাশক্তির উৎস ত্রিশূলের সাথে প্রলয় বিষাণের সন্মিলন ঘটিয়ে তরুণ সমাজের স্বপ্নকে বেগবান করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সংকল্পের দৃঢ়চেতনা নিয়ে সমাজ থেকে অন্ধকার ও কুসংস্কার দূরীভূত করে এক নতুন বিশ্ব বিনির্মাণের স্বপ্নের বীজও তিনি তরুণ হদয়ে বপন করেছিলেন। শশীকর যেমন আঁধার দূর করে চলার পাথেয় হয়, তেমনি তার কবিতাও ছিল
অন্ধকার দূর করে স্বাধীনতা আনয়নের হাতিয়ার।
গাজনের বাজনা বাজাঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানের নবম চরণে গাজন শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। গাজন শব্দটি সংস্কৃত 'গর্জন' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। ‘গাজন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল শিবের উৎসব। বান রাজা মহাদেবের তপস্যা করতেন। দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ বানের রাজ্য আক্রমণ করেন। বান রাজা যুদ্ধ প্রতিহত করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। বান রাজা ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে মহাদেবের তপস্যা শুরু করেন। এক নাগাড়ে তপস্যা করে চৈত্র মাসের শেষ দিনে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন। মহারাজের সিদ্ধি লাভের পর সঙ্গী সাথীরা ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে নাচে গানে মত্ত হন। এ গাজনের সময়ই মহাদেবের সাথে কালীর বিয়ে হয়েছিল। মহারাজের সিদ্ধি লাভের দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির শেষ দিন ঢাকঢোল বাজিয়ে শিবের গান গেয়ে চড়ক গাছের গোড়ায় গোল হয়ে দাঁড়ান ভক্তরা। শিবভক্ত সন্ন্যাসীরা শরীর ক্ষত বিক্ষত করে বড়শিতে বিদ্ধ করে চড়কগাছে ঝুলে শূন্যে ঘুরতে থাকেন। ঝরঝর করে পিঠ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। শুন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় তারা ব্যোম ব্যোম শংকর রবে গর্জন করতে থাকেন। সন্ন্যাসীদের এই গর্জন ধ্বনিই শিবসাধনায় গাজন নামে পরিচিত। চৈত্র মাসে প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর ফুলে শোভিত রূপ দেখা যায়। এই সময়েই আবার কালবৈশাখী আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। একইরকম ভগবান শিবও শান্ত অবস্থায় ভোলানাথ রূপ ধারণ করে ভক্তকে সব কিছু দান করেন। আবার ক্রুদ্ধ হলে রুদ্র রূপে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাণ্ডবলীলা চালান। কবি গাজনের বাজনা বাজিয়ে ঘুমন্ত দেশবাসীকে জেগে উঠার জন্য আহবান করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য, পরাধীনতার গ্লানিকে রোধ করার জন্য প্রয়োজনে নিজের রক্ত দেয়ার জন্য কালপুরষরূপী মহাদেবের গাজনকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
পাগলা ভোলাঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানের ১৭তম চরণে শৈব পুরাণ থেকে ভোলানাথকে উপমা হিসেবে নিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তার ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানে পাগলা ভোলা বলতে মূলত মহাদেবকে বুঝিয়েছেন। ক্রুদ্ধ কালীর হাত থেকে ধরণীকে রক্ষা করার জন্য মহাদেব ঘুমের ভান করে শশ্মান নিদ্রায় যান। কালী অজ্ঞতাবশত মহাদেবের বক্ষে নিজের পা দিয়ে আঘাত হেনে লজ্জায় নিজের জিভ কামড়ে ধরেন এবং এতে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়। সমুদ্র মন্থনে ‘হলাহল’ বিষ উঠে এলে মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষের প্রভাবে নীল হয়ে তাঁর নাম হয় ‘নীলকণ্ঠ’। নীলকন্ঠ শিবকে আপ্যায়ন করার সময় ‘ওহ মহাদেব’ বলে আকুতি করা হয়। গাঁজা বা ভাঙ নিবেদন মূলত আমাদের বদভ্যাস, মায়া, মোহ, খ্যাতি এবং কামকে সমর্পণ করা। সমুদ্রমন্থনের সময় হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব যেভাবে সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন সেইভাবে মানুষের সমস্ত পাপ বহন করে তাকে নিষ্কলুষ করার জন্য মহাদেবকে স্মরণ করা হয়।
[পৌরাণিক অভিধান, দশম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৬ পৃষ্ঠা -৪১৮]
কবি পাগলা ভোলার দ্বারা মূলত ভারতবাসীকে ক্লিব, জড়তা ও অলসতা বিসর্জন দিতে বলেছেন। অন্ধকার কুসংস্কারে নিমজ্জিত জাতি দেশের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই দেশের কল্যাণে অলসতা ও জড়তা ত্যাগ করে সবাইকে জেগে উঠার জন্যই মূলত কবি এই প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন।
হাইদরী হাঁকঃ হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জামাতা হযরত আলী (রা:) শত্রুদের উদ্দেশে রক্ত হিম করা হাঁক দিতেন। কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাকঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানের ২২তম চরণে হিন্দু কালিকাপূরাণ থেকে দুন্দুভি ঢাক শব্দটি উপমা হিসেবে নিয়েছেন। দুন্দুভি হলেন রাবনের স্ত্রী মন্দোদরার ভ্রাতা। তার পিতা ছিল কুখ্যাত ময়দানব। ময়দানব একবার মহিষের ছদ্মবেশ ধারণ করে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হন। এ মিলনের ফলে তার গর্ভে মহিষরূপী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর পরই সে গর্দভের মতো প্রচণ্ড জোরে চিৎকার শুরু করে। তার মাতা গর্ভজাত সন্তানের মুখ চেপে ধরলে নাসিকা দিয়ে গো গো শব্দ শুরু করে এবং কান দিয়ে অশ্রু বের হয়। পিতা ময়দানব পুত্রের এই অবস্থা দেখে তার নাম দেন দুন্দুভি। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাবণের নির্দেশে দুন্দুভি রাম লক্ষণকে হত্যার উদ্দেশে পঞ্চবটি বনে আসেন। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ঢাক বাজিয়ে রাম লক্ষণের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তার ঢাকের শব্দে স্বর্গ,মর্ত্য ও পাতালের সমস্ত প্রাণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বনের সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। দুন্দুভি রাম লক্ষণকে খুজেঁ না
পেয়ে বনের পশু পাখিদের উপর তাণ্ডব চালান। মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা বালি দুন্দুভির আহবান স্বীকার করে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বালি দুন্দুভিকে হত্যা করে তার দেহ ঋষ্যমুখ পর্বতে নিক্ষেপ করেন। [চতুর্থোহধ্যায়, কালিকাপুরাণ]
অসুর দুন্দুভিকে ঢাক বাজিয়ে যেভাবে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে সারা ফেলে দিয়েছিল একইভাবে ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগ্রত করানোর জন্য কবি তরুণদের কাঁধে দুন্দুভি ঢাক তুলে দিয়েছেন। কেননা মৃত্যুর আলয়কে ধ্বংস করে মুক্তজীবনের আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করার গণসংগীত একমাত্র দুর্বার তারুণ্যই গাইতে পারে। ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়িঃ কাজী নজরল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’ গানের ২৮তম চরণে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব ভীমকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে এক মহাশক্তির অবতারণা করেছেন। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে দ্বিতীয় পাণ্ডব ছিলেন ভীম। পবণ দেবতার বরপুত্র হওয়ার কারণে ভীম অসীম শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। সহস্র হস্তির বল ছিল তার শরীরে। বাল্যকালে দুর্যোধন চক্রান্ত করে বিষ মেশানো খাবার খাইয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করলে ভীম নাগলোকে পতিত হন। সেখানে নাগরাজের দেয়া বিষ পান করে ভীম অশেষ শক্তির অধিকারী হন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলে ভীম সুরঙ্গপথে সকলকে সাথে নিয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। হিড়িম্ব, বকরাক্ষস, কীচক, জরাসন্ধসহ বহু রাক্ষসকে ভীম বধ করেন। পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মৃত্যু তার হাতেই হয়। নজরুল শক্তির উৎস হিসেবে ভীমকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন মূলত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সকলকে উজ্জীবীত হওয়ার জন্য।
কাজী নজরল ইসলাম এর ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানটি একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। এ গানে ন্যায়, সত্য, জনতা ও স্রষ্টা মিত্রশক্তি এবং মিথ্যা, অন্যায় ও অত্যাচারী শাসকরূপী অসুরশক্তি-অক্ষশক্তিতে মেরুকরণ হয়েছে। শিকল পূজার পাষাণ বেদী ছিন্ন করে এ গান মানুষের হৃদয়ের কারাগারে ঠাঁই করে নিয়েছে। শত সহস্র বছর পরেও যখনই খড়গ কৃপাণের কড়াঘাতে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল ধ্বনিত হবে লাখো বিপ্লবীর কণ্ঠে দুন্দুভি দামামা বাজিয়ে উচ্চারিত হবেঃ ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট’।
তথ্যসূত্র:
১. নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, মে ২০০৬, ভাঙ্গার গান পৃষ্ঠা (১৫৯-১৬০)
২. মুজাফ্ফর আহমদ ‘কাজী নজরল ইসলাম: স্মৃতিকথা’
৩. নজরুল সংগীতবাণীর বৈভব, আমিনুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/ জুন ২০২১
৪. [চতুর্থ অধ্যায়, কালিকাপুরাণ]
৫. [পৌরাণিক অভিধান, দশম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৬
আই.কে.জে/
পৌরাণিকতায় ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’
 সুখবর এর নিউজ পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সুখবর এর নিউজ পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবরটি শেয়ার করুন