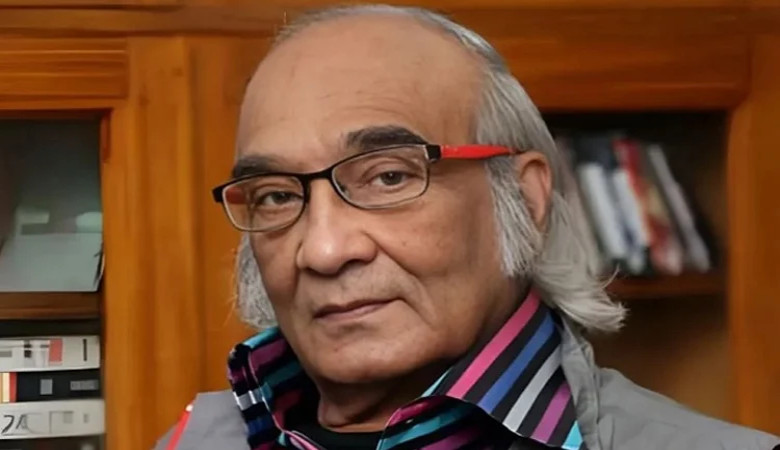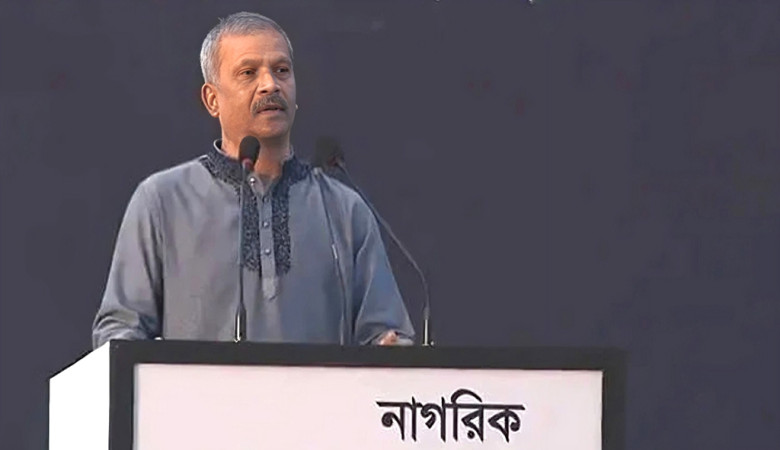পুরান ঢাকার নিমতলীতে ২০১০ সালের ভয়াবহ আগুনে অন্তত ১২০ জনের মৃত্যু হয়। এরপর বিশেষজ্ঞ কমিটি রাজধানীকে অগ্নিঝুঁকিমুক্ত করতে ১৭ দফা সুপারিশ করে। এর অধিকাংশই প্রতিপালিত হচ্ছে না। গত চৌদ্দ বছরে শুধু রাজধানীতে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, রাজধানীর ২৩ শতাংশ ভবন অতি অগ্নিঝুঁকিতে। এছাড়া ঝালকাঠির সুগন্ধ্যায় লঞ্চে আগুন, চট্টগ্রাম ও নরায়ণগঞ্জের ডিপোতে আগুন লেগে শতাধিক লোক মারা যায়।
সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সংবিধানের ১৫-১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এজন্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যাকে ১ নম্বর ‘জাতীয় সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ছাব্বিশে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, “... প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।” এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে দেশে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা তৈরি হয়। রূপরেখায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। এমন প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নীট প্রজনন হার অর্জন করা, অর্থাৎ কন্যা সন্তানের সংখ্যা স্থিতিশীল রাখা; তা সম্ভব হয়নি। এজন্য কর্মসূচিতে গতি আনতে ২০১২ সালে ফের জনসংখ্যা নীতি করা হয়।
এই নীতির রূপকল্প ছিল জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা। এর মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়া। মোট প্রজনন হার (টিএফআর) কমানো ও নীট প্রজনন হার অর্জন করা। এগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হয়নি। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার কমানো গেছে বহুলাংশে।এছাড়া আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল, যা অর্জিত হয়নি। তাই গত বছর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নতুন জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। তারা জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার পক্ষে গুরুত্বারোপ করছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি হলে দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ সুবিধার মধ্যে থাকবে। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাবে।
১৯৭৬ সালের দিকে টিএফআর ছিল ৬ দশমিক ৩। অর্থাৎ এক দম্পতি ছয়টির বেশি সন্তান জন্ম দিত। ২০২২ সালের জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ অনুসারে, দেশে এখন টিএফআর ২ দশমিক ৩। ২০১১ সাল থেকে এ হার একই জায়গায় রয়েছে। গত বছরের মধ্যে টিএফআর ২-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল, সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের বাংলাদেশ কার্যালয়ের জনসংখ্যাবিষয়ক পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ বলছে, পূর্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর সরকারের মনোযোগ ছিল। এখন জনমিতিক লভ্যাংশের জন্য জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার দিকে বেশি মনোযোগী। দেশে ১৯৮৩ সালে প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ শুরু হয়। জনমিতিক লভ্যাংশের জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারে আনতে পারলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে।
একটি দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ যদি কর্মক্ষমহীন মানুষের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে সেই অবস্থাকে জনমিতিক লভ্যাংশ বলে। জনশুমারি বলছে, দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ৬২ শতাংশ। এইসব মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। শৃঙ্খলাহীন মানুষের কারণে শহরে দুর্ঘটনা বাড়ছে।
জনসংখ্যার বর্ণনাই হলো জনমিতি বা ডেমোগ্রাফি; বেলজিয়ান পণ্ডিত আচিল গুইলার্ড ১৮৫৫ সালে সর্বপ্রথম জনমিতির সংজ্ঞা দেন। এই জনমিতি মানুষের জন্ম, মৃত্যু, লিঙ্গ, রক্ত, অনুপাত, সাধারণ প্রজনন হার, অশোধিত জন্মহার, জনসংখ্যার ঘনত্ব, বিয়ে, বিচ্ছেদ, জরা-ব্যাধি নিয়ে কাজ করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বা ডেনসিটি অব পপুলেশন বলতে আমরা বুঝি ভূমির সাথে জনসংখ্যার অনুপাত। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে বা প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তার পরিমাপকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। শূন্য জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (জিরো পপুলেশন গ্রোথ) হলো জন্ম-মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যার সমতা।
জন্ম ও মৃত্যুর পর জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ চালক হচ্ছে স্থানান্তর। স্থানান্তরকে সাবারণভাবে বুঝতে হলে, বলতে হবে- স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে সচরাচর ব্যবহৃত বাসস্থানের পরিবর্তন। স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেলে তাকে স্থানান্তর বা মাইগ্রেশন বলে। ক্ষণিকের জন্য বা অস্থায়ীভাবে কাজের উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গেলে সেটাকে বলা হয়- বিচলন বা মুভমেন্ট। জনসংখ্যা বিশারদ এভারেট লি’র মতে, বাসস্থানের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় পরিবর্তনকে স্থানান্তর বলা হয়।
১৯৪৫ সালের পর জন্ম নিবন্ধনের অধিকার জাতিসংঘের শিশু সনদে প্রথম নেওয়া হয়। জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি শিশু নাগরিকত্ব লাভ করে। ঐ সময় মৃত্যুর তথ্যও সংরক্ষণ শুরু করে বিভিন্ন দেশ। বাংলাদেশ ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন করে। ২০০৬ সালের জুলাইয়ে তা কার্যকর হয়। ২০১০ সালে ডিজিটালি তথ্য সংরক্ষিত হতে থাকে। ২০১৩ সালে প্রায় শতভাগ জন্ম নিবন্ধন শুরু হয়।
জনসংখ্যার তথ্য জানতে না পারলে কমানো কঠিন। আর জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আছে। তবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জন হয়নি অনেকখানি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন ও অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামের ভাষ্য, ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অনেক উদ্দেশ্যই পূরণ হয়নি। ব্যবস্থাপনার অবস্থা তথৈবচ’। নতুন নীতি প্রণয়নে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা ও সচেতনার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। শিক্ষিত হলেই জনগণ সচেতন হবে, আর জনসংখ্যা কমবে বলে তাদের ধারণা। ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতার আগেই সরকারি চাপে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার, বাড়ি বাড়ি ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিষেবা দিতে হবে। পাশাপাশি অন্য উপায় খুঁজতে হবে। দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের বহু দেশে উন্মুক্ত স্থানে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী রাখা হয়। স্বল্প বা বিনামূল্যে দেশের উন্মুক্ত স্থানে এসব সামগ্রী রাখতে হবে। মানুষ তা ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি ভূমিকা রাখতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের গুটমেকার ইনস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা যায়, দেশে বছরে ৫৩ লাখ গর্ভধারণ হয়। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ গর্ভধারণ অনিচ্ছাকৃত। অনেকে প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী পান না। দেশে টিএফআর অনেকটা স্থির হয়ে আছে, কমছে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার স্থির হয়ে আছে, বাড়ছে না। ফলে জনসংখ্যা কমছে না।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীর ওপর দায় চাপানো হয়। এটা ঠিক নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের আগ্রহ কম। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে ৫৫ শতাংশ দম্পতি। এর মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ পুরুষ। এটাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।
বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮শ’ কোটি ছাড়িয়েছে। বিশ্বের মধ্যে চীন ও ভারতের নাগরিক সংখ্যা বেশি। ভারত প্রথম। দ্বিতীয় অবস্থানে চীন। চীন ‘এক সন্তান নীতি’ গ্রহণ করে লোক নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। ভারতও কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। অবশ্য চীন ও ভারতের ভূখণ্ড বিশাল। তাদের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। চীন ও জাপানে লোকসংখ্যা কমছে। তাই চীন ‘এক সন্তান নীতি’ বাতিল করে লোক বৃদ্ধি করতে চাইলেও জনসংখ্যা বাড়ছে না।
চীনের নীতি বাংলাদেশে অনুসরণীয় নয়। আয়তনের তুলনায় বেশি জনসংখ্যা কোনো দেশের জন্যই কল্যাণকর নয়। আর মধ্যম আয়ের দেশের জন্য অভিশাপস্বরূপ। দেশে বেকারত্বের হার বাড়ার কারণও অধিক জনসংখ্যা। মাথাপিছু আয়ও কমে। ফলে বেকারত্ব ও মাথাপিছু আয় নিম্ন হলে সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়।
জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। দেখা দেয় খাদ্যাভাব, অপুষ্টি। বেশি মানুষের চাপে সঞ্চয় কমে, বিদেশি ঋণের পরিমাণ বাড়ে, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০১৫ সালেই ধারণা দিয়েছে উচ্চহারে বৃদ্ধি পেলে ২০৬১ সালে দেশের জনসংখ্যা হতে পারে ২৫ কোটির বেশি। মাঝারি পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে ২২ কোটি ও নিম্ন হারে বাড়লে ২০ কোটির বেশি।
১৯৭৪ সালে প্রথম জনশুমারি করা হয়। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় শুমারি হয়। এরপর প্রতি দশ বছরের পর্যাবৃত্তি অনুসরণ করে শুমারি করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে আদমশুমারি হওয়ার কথা। করোনায় পিছিয়ে যায় গণনা। ২০২২ সালে প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে ষষ্ঠ জনশুমারি করা হয়; এই শুমারি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিবিএস চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেখায় দেশের জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ১২, যা ২০১১ সালে ছিল ১ দশমিক ৩৭। দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা আট কোটি ৪১ লাখ ৩৪ হাজার ৩ জন, নারীর সংখ্যা আট কোটি ৫৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭৮৪ জন এবং হিজড়া ৮ হাজার ১২৪ জন। জনসংখ্যার মধ্যে নারী ৫০.৪৯ শতাংশ ও পুরুষ ৪৯.৫১ শতাংশ অর্থাৎ পুরুষের চেয়ে নারী সাড়ে ১৫ লাখ বেশি।
প্রথম শুমারিতে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৩ লাখ ৯৮ হাজার। ১৯৮১ সালে ৮ কোটি ৯৯ লাখ ১২ হাজার। ১৯৯১ সালে ১১ কোটি ১৪ লাখ ৫৫ হাজার। ২০০১ সালে ১৩ কোটি ৫ লাখ ২২ হাজার। ২০১১ সালের পঞ্চম জনশুমারিতে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজারে।
বিবিএস প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্বের হার ১ হাজার ১১৯ জন, এক দশক আগে ছিল ৯৭৬ জন। ৯৮ জন পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যা ১০০ জন। ১০ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৫ শতাংশ বিবাহিত।দেশে গ্রামের মানুষ ১১ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ৮০৪ জন, শহরের লোক ৫ কোটি ৩৭ লাখ ৬৩ হাজার ১০৭ জন। অর্থাৎ শহরাঞ্চলে প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ বসবাস করে। পল্লী এলাকায় থাকে ৬৮ শতাংশ মানুষ।
সিটি কর্পোরেশনে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ১২ সিটি কর্পোরেশনে ২ কোটি ১১ লাখ ২২ হাজার মানুষ বসবাস করছে। পঞ্চম জনশুমারিতে ১ কোটি ১৪ লাখ লোক ছিল। সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে, প্রায় ৬০ লাখ। ঢাকা দক্ষিণে ৪৩ লাখ। ঘনত্ব বিবেচনায় ঢাকা দক্ষিণ বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৯ হাজার ৪০৬ জন বাস করে।
অধ্যাপক মঈনুল ইসলামের ধারণা দেশে নগরায়ণ বাড়ছে। ঢাকার বাইরে ভারী শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। মানুষ কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনেও মানুষ আসছে শহরে। সেজন্য সিটি কর্পোরেশনে বসবাসের হার বাড়ছে।
কিন্তু ঢাকায় একটা সময় মানুষ কম ছিল, খোলা জায়গা বেশি ছিল। অধিকাংশ বাড়ির সামনে উঠোন ছিল। খোলাস্থানে তরুণ-তরুণীরা আড্ডা দিত, মাঠে খেলা করত। গত তিন দশকে ঢাকার উন্মুক্ত জায়গা কমতে শুরু করে। তখন মানুষ গৃহবন্দী হতে থাকে। এর থেকে মুক্তি পেতে রাতে আড্ডা দিতে মানুষ বেরিয়ে পড়ে। সুযোগ নেয় ব্যবসায়ীরা, গত এক যুগে গড়ে ওঠে অবাঞ্ছিত হোটেল-রেস্তোরাঁ। বিনোদনের জন্য হাইকিং, বাইকিং, ক্লাইম্বিং, ফিশিং ও আউটডোর প্লেয়িং কালচার গড়ে উঠেনি। এই ফাঁকে সত্তর থেকে আশির দশকে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ছড়িয়ে পড়ে দেশে।
দেশের বড় বড় শহরে আবাসিক ও বাণ্যিজিক এলাকা আলাদা করতে হবে। যেখানে বসতবাড়ি থাকবে সেখানে কার্যালয় হবে না। ঢাকায় উঁচু ভবন বেশি। উঁচু ভবনের ৯০ শতাংশই আবাসিক হবে, বাকি ১০ শতাংশ স্থান অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হবে। আবাসিক ভবন জেলখানায় পরিণত করা যাবে না। লিফটের পাশাপাশি সিঁড়ি রাখতে হবে। সিঁড়ির দরজা অগ্নিনির্বাপক হতে হবে। এ দরজা সর্বদা খোলা রাখা যাবে না। দরজা খোলা রাখলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় অক্সিজেন কমে যায়। মানুষ মারা যায়। ভবনের প্রতিটি তলায় ও কক্ষে স্মোক এলার্ম থাকতে হবে। আগুনের সূত্রপাত হলেই এলার্মের সংকতে সবাই সচেতন হতে পারে। এছাড়া আগুন নেভানোর সরঞ্জামাদি থাকতে হবে। প্রতি এলাকায় জল সরবরাহের পৃথক সঞ্চালন পথ থাকতে হবে। দমকল বাহিনীও সদা প্রস্তুত থাকবে। গ্যাস সিলিন্ডার ভবনের নিচে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।
ঢাকার পুরোনোভবন ভাঙতে হবে। খোলা জায়গা রাখতে হবে। সকল রেস্তোরাঁ বন্ধ করা যাবে না। কারণ ওখানে মানুষ শ্রম বিক্রয় করে, উপার্জন করে; অবসরে সময় কাটায়। যেন অযথা রেস্তোরাঁ গড়ে না ওঠে তার জন্য জনসংখ্যা কমাতে হবে। জনসংখ্যা কম থাকলে রেস্তোরাঁও কম হবে।
জাতীয় সংসদ ভবনের চারদিকের জায়গা অবশ্যই উন্মুক্ত করে দিতে হবে, মানুষ সেখানে যাবে। শুধু সংসদ ভবনের নিরাপত্তা কঠোর থাকবে। ঢাকার পুরোনো বিমান বন্দর উন্মুক্ত করে দিতে হবে। পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ করতে হবে, দেয়াল বিহীন সবুজ চত্বরও রাখতে হবে।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চারপাশে এখনই যেসব আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে, সেখানে হাঁটার জন্য বড় ফুটপাত, ছোট লেক, পার্ক, পিকনিক স্পট, খেলার মাঠ রাখতে হবে। স্কুল-কলেজ তো থাকবেই। বুড়িগঙ্গার জল পরিশুদ্ধ করে ভ্রমণ উপযোগী করতেই হবে। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, ময়মনসিংহ শহর গড়ে উঠেছে নদী তটে। নদীগুলোর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করিনি। আশা করছি- এ সকল কাজ করতে পারবে বর্তমান সরকারই।
অজিত কুমার মহলদার, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন। azit.mohaldar@gmail.com
আই.কে.জে/