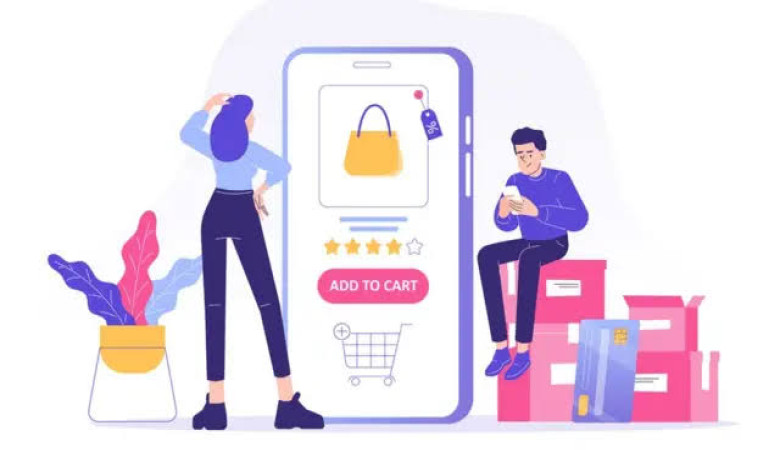ড. আতিউর রহমান, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
ড. আতিউর রহমান
সাম্প্রতিক দশকে সবচেয়ে কঠিন সামষ্টিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আপদকালীন বাস্তবতার নিরিখে আসছে অর্থবছরের জন্য সরকারি আয়-ব্যয়ের একটি চ্যালেঞ্জিং পরিকল্পনা হিসেবেই প্রস্তাবিত বাজেটকে দেখতে হবে। তবে এক বছরের বাজেট দিয়েই সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব- এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। পরিবর্তন ধীরে ধীরেই আসে। আগের বাজেটগুলোর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই এবারের বাজেট সেই পরিবর্তনের ধারাকে কতটা সহায়তা করছে সেটিই বিবেচ্য। এই পর্যালোচনায় বাজেটের দুটি দিকে আলোকপাত করতে চাই। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির ওপর বাজেটের প্রভাব এবং রাজস্ব আদায়ের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা।
প্রথমেই আলোচনা করা দরকার বাজেটে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রসঙ্গটিতে। সত্যি বলতে আসছে অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কত হবে বা না হবে তার চেয়ে মূল্যস্ফীতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে- সেদিকেই বেশি নীতি-মনোযোগ কাম্য। তবে বাজেট প্রস্তাবনায় যেমন দাবি করা হয়েছে সেভাবে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে। কারণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানাচ্ছে চলতি অর্থবছরের প্রথম এগারোটি মাসে কখনই মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে ছিল না। আর মে মাসে মূল্যস্ফীতি তো প্রায় দুই অঙ্কের কাছে ঠেকেছে (৯.৯৪ শতাংশ)। উল্লেখ্য, গত এপ্রিল পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৬৪ শতাংশ। নিঃসন্দেহে এই অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা (৭.৫ শতাংশ) তার থেকে তা বেশ বেশি। আর পাশের দেশ ভারতের চেয়ে তা প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ওপরে ছিল সর্বশেষ ২০১০-১১ অর্থবছরে (১০.৯২ শতাংশ)।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবৃতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ‘মধ্যমেয়াদে সতর্ক রাজস্বনীতি’ অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মুদ্রানীতিকেও সঙ্কোচনমূলক রাখার কথাটি বাজেট বক্তৃতায় আসেনি। তবে আগামী অর্থবছরের প্রথমার্ধের (অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩)-এর মুদ্রানীতিতে এই কথাটি রয়েছে। এর অংশ হিসেবেই সদ্য প্রকাশিত এই ষান্মাসিক মুদ্রানীতিতে বাড়ানো হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদ (রেপো) হার ৫০ ব্যাসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬.৫ শতাংশ করা হয়েছে। একইভাবে রিভার্স রেপো (স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি, এসডিএফ) ৪.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪.৫০ শতাংশ করা হয়েছে। স্পেশাল রেপো রেট (স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি, এসএলএফ) বাড়িয়ে ৮.৫০ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে কলমানি রেটের সঙ্গে রেপো রেট ওঠানামা করবে এখন থেকে।
ঋণের ওপর সুদের হারে ৯ শতাংশের বেড়াজালও উঠে গেছে। এর পরিবর্তে এখন ট্রেজারি বিলের সুদের হারের ছয় মাসের গড়ের সঙ্গে ৩ শতাংশ পর্যন্ত যোগ করে সুদ নিতে পারবে ব্যাংক। এনবিএফআইগুলোর জন্য এর চেয়ে আরও ২ শতাংশ বেশি সুদ নেওয়ার সুযোগ থাকছে। তা ছাড়া কনজুমার লোন ও সিএমএসএমই লোনের ক্ষেত্রে? সুপারভিশন বাবদ আরও ১ শতাংশ সুদ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পুরোপুরি না হলেও এই ব্যবস্থা ‘মন্দের ভালো’ বলা যায়। বাজারের ইঙ্গিত এতে মিলবে। তবে ধীরে ধীরে আরও বাজারনির্ভরতার দিকে এগোতে হবে। ডিসেম্বর নাগাদ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ব্রডমানি প্রবৃদ্ধি কমিয়ে ৯.৫ শতাংশ (জুনে ১০.৫ শতাংশ) এবং ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি কমিয়ে ১০.৯ শতাংশ (জুনে ১১ শতাংশ) লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই বেড়েছে সরকারি ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (জুনে ৪০ শতাংশ থেকে ডিসেম্বর ৪৩ শতাংশ)।
এবারের বাজেটে ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ ও সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মানোন্নয়নের কথাও বলা হয়েছে। সর্বোপরি মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতে একক মুদ্রা বিনিময় হার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা আরও আগেই একক বিনিময় হারের আহ্বান জানিয়েছিলাম। বাজারভিত্তিক এই প্রস্তাবনাগুলো যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাতে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চয়ই আশা করা যায়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমে আসতে শুরু করেছে (যেমন : জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৭০-৭৫ ডলারে নেমে এসেছে যা প্রায় করোনা মহামারী আসার আগের দামের সমান)। তবে এর প্রভাবে রাতারাতি বাংলাদেশে পণ্যমূল্য পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা ঠিক হবে না। কেননা ডলারের বিপরীতে টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে (প্রায় ২৫ শতাংশ) তার জেরে আমাদের আমদানি খরচ আগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আপাতত অসম্ভবই মনে হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি ঋণের কারণেও মূল্যস্ফীতির চাপ বহাল থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকার যে বাজেট ঘাটতি আছে তার ৫১ শতাংশই অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ করার কথা (সদ্য প্রকাশিত মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্টে তাই প্রতিফলিত হয়েছে)। সরকার যদি এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে নেয় তাতেও বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকতে পারে। তবে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, প্রচুর ডলার বিক্রি করেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনেক টাকা বাজার থেকে ফিরেও এসেছে। ফলে ব্রডমানির পরিমাণও কমে এসেছে। এতে মুদ্রানীতিকে সংযত রাখা সহজ হতে পারে। মূল্যস্ফীতি যাতে দীর্ঘমেয়াদে চেপে না বসে সেজন্য মূল্যস্ফীতির আশঙ্কাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মুদ্রানীতিকে যথার্থ সিগন্যাল বা ইঙ্গিত দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। মুদ্রাবাজারকে এই সিগন্যাল দিয়েই প্রভাবান্বিত করা সঙ্গত। সেজন্য নীতি সুদহার ও বাজারনির্ভর সুদের হারের দিকেই বাংলাদেশ ব্যাংককে হাঁটতে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আরও কিছু উদ্যোগের কথা ভাবা যায়। যেমন- আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে অনেক ভোগ্যপণ্য ও ইনপুট আমদানির খরচ এমনিতেই বেড়ে গেছে। এই বাড়তি খরচের চাপ সামাল দিতে বিদ্যমান রেগুলেটরি শুল্কসহ কিছু কিছু আমদানি শুল্ক আরও কমানোর কথা ভেবে দেখা উচিত। আশার কথা এই যে, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবৃতিতে আমদানির ওপর কড়াকড়ি কমিয়ে আনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে নিত্যপণ্য এবং দেশজ শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি ব্যাপক হারে কমে গেলে উৎপাদন ও ভোগ দুই-ই ব্যাহত হয়। তাতে সরবরাহ কমে আসে। তখন মূল্যস্ফীতি বরং বাড়ে। আর রপ্তানি শিল্পের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সে কারণেই ক্ষুদ্র আমদানিকারকদের (ধরুন পাঁচ লাখ ডলারেরও কম যারা আমদানি করেন) নির্ঝঞ্ঝাট এলসি খোলা ও ডলার প্রাপ্তির বিশেষ সুযোগ তৈরি করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এ কথাও ঠিক, মুদ্রানীতি ও রাজস্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। সেজন্য রাজস্বনীতিকেও বাস্তবানুগ রাখা চাই।
দ্বিতীয়ত যে বিষয়টিতে আলোকপাত করতে চাই সেটা হলো- প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১১ থেকে ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশের গড় রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৬২ শতাংশ (২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ৯.৯৯ শতাংশ)। সত্যি বলতে আমাদের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত অন্তত ১৫ শতাংশ হওয়া দরকার। বাজেটে ৫ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা (৮৬ শতাংশ) আহরণ করবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর। তবে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত যতটা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব হয়- তার ব্যবধান বিবেচনায় নিলে এই লক্ষ্যমাত্রাকে বেশ চ্যালেঞ্জিংই বলতে হয়। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ অর্জন করতে পেরেছে। বলা যায়, রাজস্ব আদায়ে সরকার একটি ‘কোয়ান্টাম্প জাম্প’ করতে চাচ্ছে। এমন অস্থির সময়ে এমন সাহসী উদ্যোগকে প্রশংসা না করে উপায় নেই।
সরকারি হিসাব অনুসারে টিআইএনধারী করদাতার সংখ্যা ৮৮ লাখ হলেও এদের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করছেন ৩২ লাখ। এই রিটার্ন দাখিল না করা টিআইএনধারীরা আসছে বছরে রিটার্ন দাখিল করলে রাজস্ব আয়ে প্রত্যাশিত উল্লম্ফন সম্ভব হতেই পারে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আয়কর রিটার্নধারীর সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই সরকারের মনোযোগ থাকবে। এজন্য ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার বা টিআরপি বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব রয়েছে। এতে টিআইএনধারীদের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করার প্রবণতা বাড়ার পাশাপাশি নতুন করদাতাদেরও করজালে অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করা যাবে বলে আশা করা যায়। সরকার ভ্যাটের আওতাও বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। এসবই ইতিবাচক প্রস্তাবনা।
তবে সরকার রাজস্ব আহরণকে বলশালী করতে যে পরিকল্পনা নিয়েই এগোতে যাক, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এনবিআরের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। আর এই লক্ষ্যে মনোযোগ দিতে হবে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশনের দিকে। টিনধারী সবার জন্য ন্যূনতম ২০০০ টাকা করের বিষয়টিই বিবেচনা করা যাক। করযোগ্য নয় এমন আয়কারী ব্যক্তিদেরও করের আওতায় আনাটি যৌক্তিক কিনা- সেটি আলাদা তর্ক। এ নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নও ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে এনবিআর যদি চায় বিপুলসংখ্যক নাগরিক এই ন্যূনতম কর দিক- তা হলে ডিজিটালি কর আহরণ ছাড়া সাফল্য আসবে না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যূনতম দুই হাজার টাকার কর বা চার্জ যাই বলি না কেন, ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে হয়রানিমুক্ত ব্যবস্থায় দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চালু না করাই ভালো হবে। তবে দেশপ্রেমের অংশ হিসেবে বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই মোবাইল বা অন্য কোনো ডিজিটাল আর্থিক সেবার আদলে দুই কিস্তিতে দেওয়া গেলে দেশবাসী এ প্রস্তাবে আপত্তি করবে না বলে মনে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হয়রানির আশঙ্কা দূর করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত করসীমার নিচের মানুষের ওপর এই বাড়তি চাপ দেওয়াটা কতটা যৌক্তিক হবে তা ভেবে দেখা দরকার। শুনেছি এই প্রস্তাবটি হয়তো প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তা হলেই ভালো।
এ ছাড়া ধনীদের করযোগ্য সম্পদের সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে ৪ কোটিতে উন্নীত করার বিষয়টিও পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বরং অতি ধনীদের করের হার আরও বাড়ানো যায় কিনা সে কথাটি ভাবা উচিত। উন্নত দেশে সর্বোচ্চ করহার এর চেয়ে ঢের বেশি। পঞ্চাশ-ষাট শতাংশেরও বেশি। অনেকগুলো কর প্রস্তাব দেশীয় শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে। যেমন- কাঁচশিল্প ও সুইচ/সকেট শিল্পে দেওয়া করছাড়, আমদানি করা লো ক্যাপাসিটি বৈদ্যুতিক প্যানেলের কাস্টম ডিউটি বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও আইসিটি পণ্যে ভ্যাট ছাড়ের মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি। সার্বিক বিচারে কর প্রস্তাবগুলোকে বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল মনে হয়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫ লাখ করায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবেন অনেক নাগরিক। একাধিক গাড়ির মালিকদের জন্য বাড়তি কর, টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবসার ভ্যাট উঠিয়ে দেওয়া এবং সৌরশক্তিচালিত পানিশোধন প্ল্যান্টে অগ্রিম কর প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্তগুলো পরিবেশবান্ধব উন্নয়নকে বেগবান করবে। বিভিন্ন ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রীর আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াত দেওয়ার ফলে আউট-অব-পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় কিছুটা কমতে পারে।
দেখা যাচ্ছে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব আহরণ বলশালী করা- এই দুই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্যই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাহসী পরিকল্পনা নিয়েছে আসছে অর্থবছরের জন্য। বিদ্যমান বাস্তবতায় এমন সাহসী পদক্ষেপের বিকল্প ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা দেরিতে হলেও তারা বাজারনির্ভর বিনিময় হার এবং সুদের করিডরের মাধ্যমে সময়োচিত সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। এগুলোকে সময়োচিত পদক্ষেপ বলা যায়। তবে এটাও মানতে হবে যে, এই বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমাদের গতানুগতিকতা থেকে বের হয়ে আসতেই হবে। তাই বাজেট ও মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে যুক্ত অংশীজনদের সাম্প্রতিক যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে হবে বলেই আমার মনে হয়।
ড. আতিউর রহমান : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর
আই. কে. জে/
খবরটি শেয়ার করুন