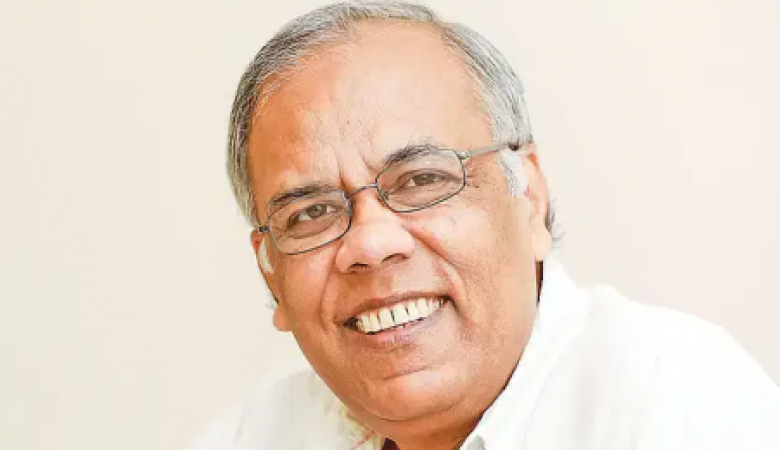শংকর মৈত্র
সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ আইন বিভাগ, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ। নিজ নিজ ক্ষমতার সীমারেখায় থেকে তিন বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার কথা বলা আছে সংবিধানে। এই তিন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণ।
কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, প্রায়ই এই সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়, বিশেষ করে যখন প্রশাসন বা নির্বাহী বিভাগ আদালতের কার্যক্রমে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।
সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো জামিন প্রদানকে কেন্দ্র করে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের চেষ্টা।
সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল হাইকোর্ট বিভাগের জামিন দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন। তার এই এখতিয়ার নিয়ে ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা। তারা বলছেন, এটা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং আদালত অবমাননা।
আইনজীবীরা বলছেন, সংবিধান ও প্রচলিত আইনের আলোকে জামিন প্রদান আদালতের বিচারিক এখতিয়ার, যা আদালত ছাড়া অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত নয়।
নির্বাহী বিভাগ এ ক্ষেত্রে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ তা করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং আইনের শাসনের মূলনীতি ভেঙে পড়ে।
জামিন হলো একধরনের বিচারিক রেহাই, যেখানে আদালত কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তদন্ত বা বিচারকালীন সময়ে নির্দিষ্ট শর্তে মুক্ত থাকার অনুমতি দেন। এটি দণ্ড নয়, বরং অভিযুক্তের মৌলিক অধিকার রক্ষার একটি ব্যবস্থা।
ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৬ থেকে ৫০২ ধারায় জামিন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এসব ধারা স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে—কোনো মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেবেন আদালত, বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।
জামিনের সিদ্ধান্ত আদালতের বিবেচনাধীন ক্ষমতা (judicial discretion)। আদালত বিবেচনা করেন অপরাধের প্রকৃতি, অভিযুক্তের সামাজিক অবস্থান, সাক্ষীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা, তদন্তের পর্যায়, এবং অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে কি না।
এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে আদালত সিদ্ধান্ত দেন জামিন দেওয়া হবে কি না। এখানে নির্বাহী বিভাগের কোনো ভূমিকা নেই, থাকার কথাও নয়।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৭, ২২, ৯৪(৪) এবং ১০৯অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা আছে: 'রাষ্ট্রের নির্বাহী ও বিচার বিভাগ পৃথক রাখা হবে।' ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বিচারকদের বিচারিক কার্যাবলিতে স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
এই দুটি ধারা থেকেই স্পষ্ট—বিচারক যখন জামিন বা অন্য কোনো বিচারিক আদেশ দেন, তা নির্বাহী বিভাগের কোনো নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা, মন্ত্রী, বা এমনকি রাষ্ট্রের প্রধানও আদালতের এ ধরনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।
এটাই আইনের শাসনের মূল কথা। বিচার বিভাগ স্বাধীন, এবং বিচারিক সিদ্ধান্তের ওপর প্রশাসনিক প্রভাব চলবে না।
কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, প্রায়ই দেখা যায়—সরকারপক্ষ থেকে জামিন বিষয়ে ‘মতামত’ প্রদানের মাধ্যমে বিচারককে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে নিম্ন আদালতে এমন হস্তক্ষেপ হরহামেশা ঘটে থাকে।
এসব কর্মকাণ্ড বিচার বিভাগের প্রতি আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, সেখানে নাগরিক স্বাধীনতাও ঝুঁকির মুখে পড়ে।
বিভিন্ন সময় দেখা গেছে রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্তেরা আদালত থেকে জামিন পেলেও, আদালতের প্রাঙ্গণেই তাদের আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্য মামলায়। এটি বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রতি প্রশাসনিক অশ্রদ্ধার চূড়ান্ত নজির।
২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়। ১৮ বছর পর এসে এখনো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হয়। মাসদার হোসেন মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।
শুধু নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচার কর্ম বিভাগ থেকে সরিয়ে আলাদা জুডিশিয়াল ক্যাডার করে জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। অগ্রগতি বলতে এইটুকুই। নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ নির্বাহী বিভাগ তথা আইন মন্ত্রণালয়ের হাতেই রয়ে গেছে। বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় করার কথা ছিলো তাও করা হয়নি।
বিশ্লেষকরা বলেন, নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে না, এটি মানবাধিকারেরও লঙ্ঘন ঘটায় এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আঘাত।
আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায় যখন কার্যকর করা হয় না বা তাকে উপেক্ষা করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়।
নির্বাহী বিভাগ যদি জামিনের সিদ্ধান্তে প্রভাব অর্থাৎ আদালতকে প্রভাবিত করে তখন নাগরিক অধিকার লুন্ঠিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন বা হয়রানি করার হাতিয়ার হয়ে উঠে । এটি গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে হরণ করে।
আদালতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড জাতিসংঘের “Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)”-এ বলা আছে: “The judiciary shall decide matters before them impartially, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences.”
অর্থাৎ, বিচারককে কোনোভাবেই রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাবের অধীন করা যাবে না। এই নীতি বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত।
বাংলাদেশও এই নীতির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ীও জামিন প্রদান আদালতের একান্ত এখতিয়ার, নির্বাহী বিভাগ সেখানে কোনো মন্তব্যও করতে পারে না।
বাংলাদেশের হাইকোর্টের একাধিক রায়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ বি এম বায়েজিদ
হাইকোর্টের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, জামিন প্রশ্নে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, “Grant or refusal of bail is a judicial act. No executive order or administrative direction can control or curtail the court’s discretion.”
অর্থাৎ, জামিন দেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা একটি বিচারিক কাজ। এ সিদ্ধান্তকে কোনো নির্বাহী নির্দেশ বা প্রশাসনিক আদেশ প্রভাবিত করতে পারবে না।
এমনকি আদালত বলেছেন—আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি আদালতের জামিন আদেশ কার্যকর না করে, তাহলে তা Contempt of Court (আদালত অবমাননা) হিসেবে গণ্য হবে। জামিন প্রশ্নে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ কেবল আইনি সমস্যা নয়; এটি নাগরিকদের স্বাধীনতার হরণ।
সংবিধানের ৩১ ও ৩৩ অনুচ্ছেদে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বৈধ প্রক্রিয়া ছাড়া কারো স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।
সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলেন, গণতন্ত্রে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভারসাম্য থাকা জরুরি।
নির্বাহী বিভাগ আইনের প্রয়োগ করে, বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তে নির্বাহী বিভাগ যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।
সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল হাইকোর্টের একাধিক বেঞ্চের জামিন দেওয়া নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন এ নিয়ে ক্ষুব্ধ উচ্চ আদালতের আইনজীবীরা। তারা প্রতিবাদ সমাবেশে করে আইন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছেন।
এ ছাড়া জামিন দেওয়ার ঘটনায় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতির কাছে যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তারও নিন্দা জানিয়েছেন আইনজীবীরা। তারা এর জন্য প্রধান বিচারপতিকে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।
আইনজীবীদের দাবি, জামিন বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে কোনো “নির্দেশনা” বা “মতামত” প্রদান বন্ধ করতে হবে। আদালতের আদেশ অমান্য করা অপরাধ—এই ধারণা আইন শৃংখলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের মাঝে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
আদালত অবমাননা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো গণতন্ত্রের প্রাণ, এবং জামিন হলো সেই স্বাধীনতার প্রতীকী প্রকাশ।
একজন বিচারক যখন কোনো অভিযুক্তকে জামিন দেন, তখন তিনি শুধু একজন মানুষকে মুক্ত করেন না—তিনি ন্যায়বিচারের নীতিকে কার্যকর করেন।
কিন্তু যদি নির্বাহী বিভাগ সেই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে, আদালতের আদেশকে অমান্য করে বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তাহলে সেটা রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর ওপরই আঘাত।
তখন সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ কেবল কাগজে থাকে, বাস্তবে হারিয়ে যায়। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা অনেক চড়াই–উতরাই পেরিয়ে এসেছে। এখন সময় এসেছে সেই অর্জনকে রক্ষা করার।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানে কেবল বিচারকদের স্বাধীনতা নয়—এটা নাগরিকের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের সততার প্রতীক। জামিন আদালতের এখতিয়ার, আদালতের আদেশ মানা মানে আইনের শাসনকে সম্মান করা।
আর আইনকে সম্মান করা মানে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা। আজ ৪ঠা নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন। আইনজীবীদের প্রত্যাশা, এই সভায় বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন উচ্চ আদালতের বিচারকরা।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, কলামিস্ট।
খবরটি শেয়ার করুন